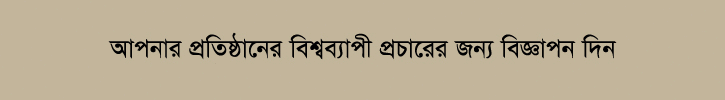জাগো হুয়া সাভেরা

- আপডেট সময় শুক্রবার, ২৪ জুন, ২০২২

এ চলচ্চিত্রটি দেখার গোপন ইচ্ছা নিয়ে বসে ছিলাম বহুকাল। সেই আশির দশকে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময় থেকেই এ চলচ্চিত্রটি নিয়ে শুনে আসছি নানা কৌতূহলোদ্দীপক কথা। ১৯৫৮ সালে তৈরি জাগো হুয়া সাভেরা ছবিটিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান আর ভারতের অসাধারণ সব কলাকুশলীর মিলন ঘটেছিল। ছবিটি নির্মিত হয়েছিল উপমহাদেশের রাজনীতিরও এক ক্রান্তির সময়ে। বাংলা সাহিত্যের অনন্য লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। পরিচালনা করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানেরই নামজাদা চলচ্চিত্রকার এ জে কারদার। আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছবির সহকারী পরিচালক ছিলেন জহির রায়হান। প্রধান চরিত্রে ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভিনেতা খান আতাউর রহমান আর কাজী খালেক। ছিলেন কলকাতার গণনাট্য সংস্থার বিখ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। সংগীত পরিচালনায় ভারতের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ তিমির বরণ। ক্যামেরায় ছিলেন অস্কার বিজয়ী ব্রিটিশ চিত্রগ্রাহক ওয়াল্টার লাসালি। সব মিলিয়ে বলতে হয় এক মহাযোগই ঘটেছিল এ ছবিতে। জাগো হুয়া সাভেরা মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছিল, প্রতিযোগিতা করেছিল অস্কারের জন্যও। কিন্তু ছবিটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ হয়ে যায় মুক্তির পরপরই। সে বছরই পাকিস্তানে সামরিক শাসনের ঘোষণা দেন আইয়ুব খান এবং ছবিটি নিষিদ্ধ করেন ‘কমিউনিস্ট ভাবধারা’র অভিযোগে। তারপর হারিয়ে যায় ছবিটি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ফ্রান্সের এক চলচ্চিত্র উৎসবের আর্কাইভ থেকে এটি উদ্ধার করেন ছবির প্রযোজক নোমান তাসিরের ছেলে আনজুম তাসির। ২০১৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ল্যাসিক চলচ্চিত্র পর্বে দেখানো হয় এ ছবি। অবাণিজ্যিকভাবে ছবিটির কিছু প্রদর্শনী হয় ব্রিটেনে, বাংলাদেশেও। নির্মাণের প্রায় ৬০ বছর পর সেই আলোচিত ছবি দেখার সুযোগ ঘটল সম্প্রতি।
জাগো হুয়া সাভেরা দেখার পর একাধারে তৈরি হলো মুগ্ধতা আর খটকা। খটকার কথায় পরে আসি। প্রথম মুগ্ধতা ছবির চলচ্চিত্রায়ণে। জোবরা দ্য গ্রিক চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণের জন্য পরবর্তীকালে অস্কার পাওয়া ওয়াল্টার লাসালির ক্যামেরার প্রতিভা টের পাওয়া যায় জাগো হুয়া সাভেরার প্রতিটি দৃশ্যে। সাদা-কালো এ ছবিটির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে ঢাকার কাছে মুন্সিগঞ্জ এলাকার এক গ্রামে। সাদা-কালো ছবির বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকে, থাকে সম্ভাবনাও। আমরা পৃথিবীকে সাদা-কালোতে দেখি না; রং চলে যাওয়াতে সাদা-কালো ছবির চরিত্র, বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কগুলো হয়ে ওঠে আরও নিবিড় ও স্পষ্ট। বস্তু ও প্রাণের বাইরে যে স্পেস সেটির দিকে আমাদের মনোযোগ আরও নিবিষ্ট হয়। পরিবেশের নানা আকার ও প্যার্টান দৃশ্যমান হয়ে ওঠে প্রবলভাবে। সাদা-কালো ছবির সেই শক্তিকে দুর্দান্ত ব্যবহার করে ৬০ বছর আগের বাংলাদেশকে চোখের সামনে জ্যান্ত করে তোলেন লাসালি। তবে বাংলার গ্রাম প্রান্তরের চমৎকার বৈচিত্র্য, দরিদ্র ঘরের স্থাপত্য, বাঁশের ভেতর পয়সা রাখার গোপন নি¤œবর্গীয় ব্যাংক, দড়ির ভেতর গিঁট দিয়ে সেটিকেই বানিয়ে ফেলা হিসাবের খাতার মতো তাদের জীবনযাপনের ছোটখাটো অনুষঙ্গ, প্রাণচঞ্চল গ্রাম্য মেলার নিবিড় খুঁটিনাটি—এসব লাসালি বা কারদারের চোখ থেকে আসার কথা নয়। এ নির্ঘাত সহকারী পরিচালক আমাদের জহির রায়হানেরই কাজ। ছবির পাত্রপাত্রীরা একসময় ঢাকা শহরে এলে চকিতে দেখার সুযোগ হয় পঞ্চাশ দশকের ঢাকাকেও। রাস্তাঘাট, পোশাক, ঘরবাড়ি, জীবনযাপন এতটাই বাহুল্যহীন যে দেখে মনে হয় যেন অন্য কোনো গ্রহ।
পরিচালক কারদারের মুনশিয়ানাও স্পষ্ট ছবিজুড়ে। রাতের নদীতে মাছ ধরার এক চমৎকার দৃশ্যে শুরু হয় ছবি। নেপথ্যের সুরে চলে বইঠার মৃদু ছলচ্ছল ছলচ্ছল, অন্ধকারে নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো নৌকার মাঝিদের ভেতর চলে মাছ ধরার খবরাখবর বিনিময়। বড় প্রেক্ষাপট থেকে এরপর আমরা আসি একটি বিশেষ নৌকায়। সেখানে জাল টেনে ওঠায় মাঝি, পাটাতনে ছড়িয়ে রাখে জালে ধরা পড়া মাছ। ক্লোজ আপে আমরা দেখি মৃতপ্রায় বড় দুটো মাছ গভীর নিশ্বাস নিয়ে হাঁপাচ্ছে। এরপরই দেখতে পাই জাল টেনে তোলা ক্লান্ত দুই মাঝিও ঠিক একই ভঙ্গিতে হাঁপাচ্ছে। মাছের হাঁপানোর সঙ্গে মাঝির হাঁপানোর জাকস্টাপোজ, জীব আর মানুষের বেঁচে থাকার এই সমাপতন, একটা নতুনতর ব্যঞ্জনা তৈরি করে। চোখ এড়ায় না ছবির মেধাবী সম্পাদনা। চারদিকে তখনো রাত। দূরে দূরে জেলে নৌকার বাতি। এক রহস্যময় বেদনাঘন পরিবেশ যেন। কারদার ছবি শুরু করেন কাহলিল জিবরানের কবিতা দিয়ে:This is the path of the spirit paved with thorns and stones. This is manÕs shadow. This is night, but morning will come„মনে রাখা দরকার, এই ছবি যখন তৈরি হচ্ছে তার কাছাকাছি সময়ই হলিউডের স্টুডিওভিত্তিক গ্লামারকেন্দ্রিক ছবির বাইরে শুরু হয়েছে নিউ রিয়েলিস্ট ধারার চলচ্চিত্র। ইতালিতে ডি সিকা বানিয়ে ফেলেছেন বাইসাইকেল থিভস এবং জাগো হুয়া সাভেরার ঠিক বছর তিনেক আগে তৈরি হয়েছে ভারতের সবচেয়ে সফল নিও রিয়েলিস্ট ছবি পথের পাঁচালী। সে হিসেবে এ জে কারদার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অগ্রযাত্রার একেবারে সামনের সারিতেই ছিলেন তখন।
মুগ্ধতা আছে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের চিত্রনাট্য নিয়েও। বাম ঘরানার লেখক ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ যে চিত্রনাট্যের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কাছে যাবেন, তা বোধগম্য। তিনি হয়তো হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ ছবিতে কপিলা, কুবের, হোসেন আলী নেই, আছে মালা, কাশেম, লাল মিয়া। পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের যাবতীয় বহুমাত্রিকতা না থাকলেও জাগো হুয়া সাভেরার চিত্রনাট্যে ঘটনা, ভাবনার নানা সূক্ষ্ম দোলচাল বজায় রেখেছেন ফয়েজ। পদ্মা নদীর মাঝির ছায়া রেখে জেলে জীবনের সংগ্রাম, ক্লান্তি, প্রেম ও বঞ্চনার মন ছোঁয়া একটা গল্প বলেছেন তিনি; বিশেষ করে এমন একটা সময় তিনি গল্পটা বলছেন, যখন বাম ধারার শিল্প-সাহিত্যে চলছে ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ’-এর একটা জোর তৎপরতা। একধরনের উগ্র যান্ত্রিক মার্ক্সবাদের প্রয়োগে তখন চলছে শোষণ-বঞ্চনার শিল্প-সাহিত্য। কিন্তু ফয়েজ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সেই সব প্রবণতার বাইরে একটা মৃদু অথচ তীব্র মানবিক গল্প শুনিয়েছেন ছবিতে। দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করেছেন ঘটনার নাটকীয়তা। মনে পড়ে, ছবির চমৎকার শেষ দৃশ্য। মূল চরিত্র মাঝি মিয়ার শালী মালার সঙ্গে তার সহযোগী, স্নেহের পাত্র এতিম কাশেমের মন দেওয়া-নেওয়ার খবরে তোলপাড় গ্রামবাসী, ক্ষুব্ধ মিয়া নিজেও। ছবির শেষে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় জর্জরিত মিয়া যখন আবার মাছ ধরতে রাতের নৌকায় উঠছে, তখন পেছনে থেকে কাশেম তাকে ডাক দেয়, কিন্তু মিয়া পেছন ফিরে তাকায় না। শুধু থমকে দাঁড়ায়। কাশেম বলে, ‘ভাই, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।’ মিয়া কিছু বলে না। দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর তার মুখে একটা মৃদু হাসি দেখা যায়। কাশেমের দিকে পেছন ফিরেই বলে, ‘তোর ভাবির সাথে আলাপ কর।’ বলেই নৌকায় উঠে যায় সে। এতে অপ্রত্যাশিত আনন্দ দেখা দেয় কাশেমের মনে। সে ছুটে যায় মালার কাছে। বলে, ‘ভাই আমাদের বিয়েতে রাজি।’ মেধাবী সংলাপের কারুকাজে গভীরতর বেদনার এক গল্পের ভেতর অপরূপ এক মানবিক মুহূর্তের জন্ম দেন ফয়েজ। চমৎকার অভিনয় করেন কাশেম চরিত্রে খান আতাউর রহমান, যিনি তখন আনিস নামে পরিচিত এবং মালা চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র। মিয়া চরিত্রে অভিনয় করা জুরাইন রক্ষী পাকিস্তানি না ভারতীয় অভিনেতা, জানি না; তবে তিনি নিঃসন্দেহে শক্তিমান।
কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষই তো একটি শিল্পকর্ম বিচারের একমাত্র শর্ত নয়; বরং খুব গুরুত্বপূর্ণ এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতাও। খটকা সেখানেই। ছবির ভেতরের ব্যাকরণ শ্রেণি শোষণের মার্ক্সবাদী ধ্রুপদি ধারার কাঠামোতেই। সেই রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন এর সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা নিয়ে। বাংলার এক মাঝি পরিবারের পাত্রপাত্রী যখন উর্দু ভাষায় কথা বলে, এ অঞ্চলের জেলে জনপদের সব চরিত্র যখন হয়ে পড়ে শুধু মুসলমান, তখন সেটা গভীর খটকার জন্ম দেয়। তিমির বরণের অসাধারণ সংগীত আয়োজন সত্ত্বেও বাংলার মাঝির বইঠা বাওয়ার প্রেক্ষাপটে উর্দু গান কানে বেমানান লাগে। শুনেছি নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ছবিটি কয়েক দিন প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল, তবে দর্শক মোটেও সাড়া দেয়নি।
পূর্ব পাকিস্তানের দর্শকদের জন্য ভাষার দূরত্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের দর্শকদের জন্য ল্যান্ডস্কেপ—জীবনযাপনের দূরত্ব ছবিটির আবেদন তৈরির ক্ষেত্রে বড় বাধা হওয়ারই কথা। বাংলার বিখ্যাত এক উপন্যাসকে কেন্দ্র করে, বাংলার কলাকুশলীদের নিয়ে এ ছবি কেন বাংলায় হবে না—এ প্রশ্ন প্রবলভাবে জাগে, বিশেষত যখন এর বছর খানেক আগেই ঘটে গেছে রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন। বাংলায় তৈরি ছবি উর্দুতে ডাব হতে পারত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিচালকেরা উর্দুতে ছবি তৈরি করেছেন; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পরিচালকেরা বিপরীতটা করেছেন বলে জানা যায় না। বোঝা যায় সে সময়ের ভাষা ও রাজনীতির আধিপত্যের রসায়ন। এ বিষয়ে এই ছবির কলাকুশলীদের ভেতরে নেপথ্যে কী ধরনের মোকাবিলা হয়েছিল, সেটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক রহস্য হয়ে রইল। অবশ্য এ ছবির কলাকুশলীদের বহুদিন পর মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। জহির রায়হান সরাসরি যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় কারদার ও খান আতার ভূমিকা বিতর্কিত। জাগো হুয়া সাভেরা এই উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য কিন্তু স্ববিরোধী একটি ছবির উদাহরণ, যা নন্দনতাত্ত্বিকভাবে অসাধারণ, সাংস্কৃতিকভাবে বেখাপ্পা। ( দৈনিক প্রথমআলো অনলাইনের সৌজন্যে)