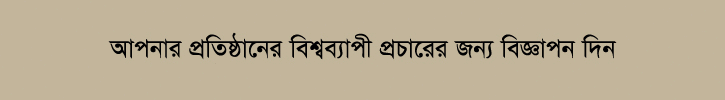সৈয়দ মুজতবা আলী: গল্পের মানুষ

- আপডেট সময় শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের বাংলা ভাষার অভিধানে ‘কিংবদন্তী’ শব্দটির অর্থ এভাবে দেওয়া হয়েছে: লোক-পরম্পরায় কথিত ও শ্রুত বিষয়। তাহলে কারও পক্ষে কিংবদন্তীর বিষয়ে পরিণত হতে হলে লোকপরম্পরার একটি দীর্ঘ সময়ক্রম প্রয়োজন। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলী যে তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীর চরিত্রে পরিণত হলেন, সেটি কী প্রকারে? যাঁরা মুজতবা-সাহিত্য পড়েছেন, তাঁদের কাছে উত্তরটি সোজাÍকিংবদন্তী শব্দের ভেতরে বদ্ বা বলার যে বিষয়টি আছে, সেই ‘বলা’ই তাঁকে এই মহিমা দিয়েছে। তিনি বলে গেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাস-কাহিনিগুলো, তাঁর মতো করে; মানুষ তাঁকে নিয়ে বলে গেছে তাদের যা বলার তা; এবং এক (লোক) প্রজন্মে তিনি অর্জন করেছেন এক ঈর্ষণীয় উচ্চতা, যে উচ্চতায় কিংবদন্তীর চরিত্রেরা উড়ে বেড়ায়।
তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি, তাঁর মেজাজ, তাঁর শৈলী, তাঁর ঐশ্বর্য অননুকরণীয়। তিনি পরিশীলিত ভাষার চর্চাকারী, রবীন্দ্রনাথের ভাষা তিনি কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন অনেক সাধনায়, তাঁর অধিকারে ছিল ভাষার অহংকারী সব নির্মাণ ও ভাষার লিখিত রূপের মেধাবী প্রকাশ। কিন্তু সেই তিনিই অবলীলায় বিচরণ করতেন কথ্য ভাষার অলিগলিতে, মৌখিক সাহিত্যের পথেপ্রান্তরে। ফলে তাঁর ‘বলা’ ছিল বৈশিষ্ট্যমত।
মুজতবা আলী অনেকগুলো ভাষা জানতেন, কিন্তু ভাষার পা-িত্য দেখানো ছিল তাঁর প্রবৃত্তির বাইরে। ভাষা শিখে তিনি যা করেছেন: ওই সব ভাষার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বয়ানগুলো অভিনিবেশ নিয়ে পড়েছেন। এক ভাষার লেখা সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভাষার সাহিত্যের তুলনা করেছেন; ভাষার প্রাণ ও ভাষার অন্তর্গত গান খুঁজে বেড়িয়েছেন; ভাষার মানুষি আদলটি পরম যতে, উন্মোচিত করেছেন। চিহ্নিত করেছেন ভাষার ভেতরের শক্তিকে, ভাষার প্রতিরোধ-প্রতিবাদের ক্ষমতাকে।
এ জন্য সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর সক্রিয়তা। তাঁকে কেউ ভাষাসংগ্রামী বলে ডাকেনি, ডাকলে সেই অভিধা তাঁকে কিছুটা আমোদই দিত, যেহেতু তিনি বলতেন, যে ভাষায় সংগ্রামের ইন্ধন নেই, প্রাণের প্রাচুর্য আর সুধা নেই, সেই ভাষায় কোমল-মধুর গান গাওয়া যায় কিন্তু জীবনের কথাগুলো বলিষ্ঠভাবে বলা যায় না। বাংলা ভাষার ‘আঞ্চলিক-লৌকিক-প্রমিত-পরলৌকিক’ সব রূপ দেখেছেন বলে তিনি গর্ব করতেন (পরলৌকিক? হ্যাঁ, তিনি বলতেন, পরকালের কথা বয়ান করতে গিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষ নিজের ভাষার ওপর একটুখানি গোলাপজল নাহয় গঙ্গাজল ছিটিয়ে পরিশ্রুত করে নেয়)। সেই বাংলার মর্যাদার প্রশ্নে তিনি লড়লেন, পাকিস্তানিদের চক্ষুশূল হলেন ও দেশান্তরে গেলেন!
‘মুজতবা-জীবনে পরবাস’ শীর্ষক একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভই তো লেখা যায়। পরবাস কীভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছে? অনেক উপায়ে: তাঁকে নিঃসঙ্গতা দিয়েছে, যা তাঁকে নিজের কাছে স্থিত অথবা অস্থিত করেছে; একসময় তাঁকে শুধু নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে শিখিয়েছে। ফলে তাঁর ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যেসব অপূর্ণতা অথবা বিচ্যুতি ছিল, সেসব নিয়ে তিনি কোনো আক্ষেপ করতেন না। পরবাস তাঁর অন্তদৃর্ষ্টি খুলে দিয়েছে। সেই দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন বস্তু-প্রকৃতি-মানুষের ভেতরের জীবন-ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় ঃযব ষরভব ড়ভ ঃযরহমং। পরবাস তাঁকে শিখিয়েছে মানুষকে পড়তে, সহনশীল হতে এবং কৌতুক ও রসবোধের অস্ত্রটিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে। এক কথায় বলা যায়, মুজতবা আলীকে মুজতবা আলী হয়ে ওঠার জন্য এই পরবাসের প্রয়োজন ছিল।
পায়ের নিচে তাঁর সরষে ছিল ছোটবেলা থেকেই। তা না হলে শান্তিনিকেতনে পড়ার ভূত তাঁর মাথায় এমনভাবে চাপত না। শান্তিনিকেতন তো লাউয়াছড়া নয় যে মৌলভীবাজার থেকে দুই ঘণ্টায় একটা চক্কর দিয়ে আসা যায়। তাঁর মুজতবা আলী হয়ে ওঠার জন্য শান্তিনিকেতনের বিকল্প ছিল না। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের বিকল্প ছিল না। শান্তিনিকেতনে এসে তিনি জাতীয়তার একটা পাঠ পেয়েছেন, যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল, আপত্তি ছিল। শান্তিনিকেতনে তিনি হিন্দু-মুসলমান বিভাজনও দেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসান্নিধ্য তাঁকে এসবের বহিঃস্থ প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে অন্তরের মিলগুলো খুঁজতে সাহাঘ্য করেছে।
আঞ্চলিকতা নিয়েও যথেষ্ট অভিমান ছিল মুজতবা আলীর। তিনি আজীবন সিলেট-সমর্পিত মানুষ ছিলেন। আমাদের সঙ্গে যখন কথা বলতেন, যে সিলেটি ব্যবহার করতেন তার তুলনা অন্য কারও চর্চায় আমি পাইনি। তিনি বলতেন, তাঁর ভাষাটি ছিল ন্যাপথলিনের যতে, সুরক্ষিত তোরঙ্গে তোলা সিলেটি, যেহেতু এর ব্যবহার প্রতিদিন তাঁকে করতে হতো না। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বৈশ্বিক।
তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক মানুষ খুব কমই ছিলেন বঙ্গদেশে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে আমি তুলনা করি। নেতাজির মতো অবিচল স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁর, যদিও বিশ্বের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই তাঁর ছিল স্বাচ্ছন্দ্য। তিনি বিশ্বকে মাপতেন হাত দিয়ে, নিজেকে ডুরি আঙুল দিয়ে। কারণ, তিনি নিজেকে নিয়ে বড়াই করতে পছন্দ করতেন না। ইউরোপীয় সাহিত্যে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গসাহিত্যের প্রকাশ হয় প্রধানত দুই প্রকারে এক জুভেনালের আদলে, যেখানে শাণিত, অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণই প্রধান হয়ে ওঠে। আরেক হলো হোরেসের পন্থায়, যেখানে রসবোধটাই প্রধান, হাসতে হাসতে সংশোধনটাই প্রধান। তিনি হোরেসের অনুসারী ছিলেন, হাসতেন মাথা দিয়ে, সূক্ষ্ম কৌতুকরসের সঞ্চার করে, নানান কিছুর মধ্যকার অসংগতিকে বেঢপ আকৃতিতে সাজিয়ে, শব্দের প্রাণিত-শাণিত খেলায় মেতে। কথার পিঠে কথা সাজানো ছিল তাঁর সহজাত একটি প্রতিভা। ইংরেজিতে যাকে ঢ়ঁহ বলে, সেটি ছিল তাঁর ট্রেডমার্ক।
মুজতবা আলীর লেখালেখিতে রম্য ও রসের যে উপস্থিতি, তা কখনো মাত্রাতিরিক্ত নয়। কোন কথায়, কতটা কথায়, কোন প্যাঁচে কে কতটা হাসবে এবং হাসতে হাসতে ভাববে, নিজেকে মাপবে, সেই রসায়ন তিনি জানতেন। তাঁর এই পরিমিতিবোধ ছিল অসামান্য। তিনি বলতেন, মোনালিসা যে এত অবিস্মরণীয় এক চিত্রকর্ম, তার পেছনে দা ভিঞ্চির আঁকিয়ে-হাতের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তাঁর পরিমিতিবোধ। ব্রাশের একটা অতিরিক্ত সঞ্চালন ছবিটির রহস্য কেড়ে নিত। একজন রম্যলেখকেরও থাকতে হবে সেই জ্ঞান, তালে-ঠিক কোনো মদ্যপায়ীর মতো, ঝানু জুয়াড়ির মতো।
বাংলা সাহিত্যে মুজতবা আলীর পাকাপোক্ত স্থান রম্যলেখক হিসেবে। কিন্তু এটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। মুজতবা-গবেষক নূরুর রহমান খান (মুজতবা-সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী, ঢাকা ২০১০) সেগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন এভাবে: ক. হাস্যরস-প্রধান গল্প, খ. করুণ রসাত্মক গল্প, গ. বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক গল্প, ঘ. প্রণয়মুখ্য গল্প, ঙ. অম্লমধুর গল্প, চ. ভয়ংকর রসের গল্প। ভয়ংকর রসের গল্প অবশ্য মাত্র একটি, ‘রাক্ষসী’, যেখানে এক বৃদ্ধার মৃতদেহের বর্ণনা সত্যিই ভয়ংকর। মুজতবা আলীর গল্পগুলোর কাহিনি ও বিস্তার এবং এদের অন্তর্গত জগৎটি বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের একটি কারণ তাঁর ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা। নানা দেশে গিয়েছেন তিনি, অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার সামনাসামনি হয়েছেন, বিচিত্র সব মানুষজন দেখেছেন, শুনেছেন তাদের গল্প। ফলে তাঁর সাহিত্যের জগৎ হয়েছে বহু স্তরে বিন্যস্ত, বহু রেখায় নির্ণিত। আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার কম্পাস সে জগতের হদিস করতে পারে না।
সৈয়দ মুজতবা আলী গল্প-উপন্যাস লিখতেন, কিন্তু বলতেনই আসলে। ছোটগল্পগুলোর কথা নাহয় তোলা থাক, সেগুলোতে বলার মেজাজটা সহজেই ধরা যায়। কিন্তু যে চারটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার তিনটিতেই তো এক অসাধারণ কথনভঙ্গির কারুকাজ। শেষ উপন্যাস তুলনাহীনা প্রথম তিনটির তুলনায় কিছুটা বিক্ষিপ্ত, যেহেতু এর ঘটনাপ্রবাহ ১৯৭১-এর পটভূমিতে স্থাপিত, যা ছিল ঘটনাবহুল-বীরত্ব আর কাপুরুষতা, হত্যা ও মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগের বিপরীতধর্মী ঘটনায় পূর্ণ। কিন্তু প্রথম তিনটি উপন্যাস ঠাসবুনটে লেখা।
সেই তিনটি উপন্যাস পড়ে আমার মনে হয়েছে, যত না গল্পকাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা, তার চেয়ে বেশি ভাষার সাবলীলতা উপন্যাসগুলোকে গতিশীল করেছে। মানুষ যখন কথা বলে, তার একটা ছন্দ-লয়-তাল এবং গতি-দ্রুতি থাকে। এ তিন উপন্যাসেও তাই আছে। তাঁর গল্প বলায় লঘু-গুরু, বিদেশি-দেশি ভাষা, পরিচিত-অপরিচিত দৃশ্যপট মিলেমিশে যায়। সানন্দে এই প্রক্রিয়ার সহযাত্রী হন পাঠক। আমার বিশেষ প্রিয় শবনমÍতাঁর স্বাক্ষরযুক্ত একটি কপি আমার আছে সে জন্য অবশ্যই, কিন্তু বড় কারণ শবনম–এর চরিত্রায়ণের কুশলতা, যা মনে দাগ কেটে যায়। তবে হয়তো শুধু তা-ই নয়, হয়তো এ জন্য যে, এ উপন্যাসের নায়ক মজনুনকে আমি চিনতে পেরেছিলাম।
জীবন যখন উপন্যাসে চলে যায় এবং ওই জীবন-চরিত্রে লেখকের বিনিয়োগও বাড়ে, তখন উপন্যাস তো জীবনকেই ছাড়িয়ে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী অনেক বিষয়ে লিখেছেন, অনেক কিছু করেছেন। বিচিত্র তাঁর অর্জন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন গল্পের মানুষ হিসেবে। গল্প বলেছেন এত কুশলতায়-রসে-রঙ্গে-প্রেমে পূর্ণ সে বলার জাদু একটা মোহের বিস্তার ঘটায় প্রতিটি পাতাজুড়ে। আড্ডায়, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, বক্তৃতায়, সাক্ষাৎকারে, লেখালেখিতে ছিল তাঁর সেই জাদুবিস্তারী প্রতিভার ছোঁয়া।