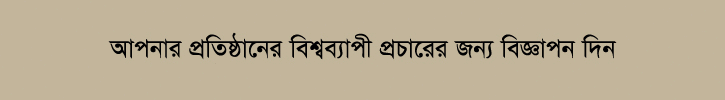দাও ফিরায়ে সে তাওয়াপিঠা

- আপডেট সময় শুক্রবার, ১৭ মার্চ, ২০২৩

১৪ শাবান ৭ মার্চ ২০২৩ পবিত্র শবেবরাত পালিত হলো। বরকতময় রজনীটা এখন অনেকটা নীরবেই আসে নীরবেই চলে যায়। ফেসবুকে কালের কবলে হারিয়ে যাওয়া তাওয়াপিঠার কথা লিখতেই বাজার থেকে আওলাচালের গুঁড়ি নিয়ে আসে তওহিদ (ছেলে)। আমাদের ছিল চর এলাকা। প্রধান ফসল ধান। পৌষ পার্বণসহ যাবতীয় উৎসবের মূল উপাদান চাল। শৈশবে ঘরে ঘরে আওলাচালের গুঁড়ি পেষতে দেখলেই বুঝতে পারতাম, শবেবরাত সমাগত। সবচে’ নিচু জমিতে লেঞ্জা আমন ধান বপন করতেন বাবা। কাটতেনও সব ধান কাটার পরে। ধানের লম্বা লেজ ছিল বলে লেঞ্জা আমন নামকরণ। এই ধানের কাঁচা চাল ঈষৎ মিষ্টি। কৃষাণীরা সারা বছর পিঠা-চিঁড়া খাওয়ার জন্য এই ধানটাই সংরক্ষণ করতেন। কাঁচা চালের আরেক পরিচয় আলাচাল। আলাচালের খামির থেকে বৃত্তাকারের পিঠা ‘তাও’ দিয়ে ছেঁকা হয় বলে ‘তাওয়াপিঠা’। ‘রুটি’ শব্দটি শহর থেকে গাঁয়ে ঢুকেছে। গাঁয়ের মানুষের কাছে, গমের আটা বা ময়দা দিয়ে কারখানার প্রস্তুতকৃত নানা আকারের খাবারের নাম রুটি বা বিস্কুট। রুটি-বিস্কুট হাট-বাজারে বেচাকেনা হয়। রেশনিং পদ্ধতিতে পাওয়া গমের আটা দিয়ে বানানো পিঠা খাওয়ার প্রচলন শহরে কবে শুরু হয়েছিল, মনে নেই। ষাটের দশকে এলাকায় গম চাষ শুরু। গমের স্থানীয় নাম গেউ। গ্রামে গমের আটা থেকে প্রস্তুতকৃত রুটির নামও ছিল আটার পিঠা। শহরের সাথে গাঁয়ের যোগাযোগ সহজ হওয়ার কোনো এক সময় ‘তাওয়াপিঠা’ নামটি বদলে হয় ‘তাওয়ারুটি’।
তাওয়াপিঠা নির্মাণ পদ্ধতিও জটিল। অসিদ্ধ লেঞ্জাধান রৌদ্রে টানটান করে শুকিয়ে কাহাইল-সিয়াইট দিয়ে ছাঁটার পর সাদা ধবধবে চালের নাম আল্লাচাল বা আলোচাল (আতপ)। আল্লাচাল পুনরায় কাহাইল-সিয়াইটে কিংবা ঢেঁকিতে তুলে ধুনাধুনা করা হয়। ধুনাধুনা করা চালচূর্ণ চিকন চালুনি দিয়ে ছেঁকে বের করা হয় পাউডার। মিহি পাউডারের মতো অংশের নাম ‘গুঁড়ি’। বড় পাতিলে পানি ফুটিয়ে ফুটন্ত পানিতে দুই হাতে দলা-দলা করে গুঁড়ি ছাড়তে হয়। পরিমিত পরিমাণ সিদ্ধ হওয়ার পর দলাগুলো পুনরায় তুলতে হয় কাহাইলে। সিয়াইট দিয়ে মনের মতো পেষার পর প্রস্তুত হয় খামির বা খাম্বির। ৮-১০ সের আল্লাচালের গুঁড়ি থেকে বানানো গোলাকার খাম্বিরের পি- দেখতে ঠিক ফুটবলের মতো। আল্লাচাল থেকে খাম্বির পর্যন্ত পৌঁছতে উঠতি বয়সী দু-তিনজন মেয়ের রাত পার হয়ে যায়। সকাল থেকে বেলুনে পিঠা বেলা ও সেঁকা শুরু। এক দিকে ভেজা গামছা দিয়ে ঢাকা প্রকা- ফুটবল আকারের খাম্বিরের চার পাশে পিঁড়ি-বেলুন হাতে বেলতে বসে যায় তরুণীরা, অপর দিকে কয়েক চুলায় সেঁকতে শুরু করে কেউ কেউ। আমার দায়িত্ব ছিল, বেলা পিঠা সেঁকার জন্য চুলার কাছে পৌঁছে দেয়া। খাম্বির থেকে তাওয়াপিঠা ছাড়াও বানানো হয় দউল্লাপিঠা, লোনপিঠা ও কুলিপিঠা (সমুচার আকৃতি, ভেতরে নারিকেল-গুড়সহ গরম মসলা)। মেয়েদের কেউ কেউ বানাতো কারুকার্যময় নকশিপিঠা। খেজুর গাছের কাঁটা, ছুরি-চামচ ইত্যাদির সাহায্যে ভারী রুটির ওপর মেয়েদের আঁকা শৈল্পিক কারুকাজের ভেতর ভেসে উঠত বাঙালি লোক সংস্কৃতির শাশ্বত চিত্র। চালের গুঁড়ির খাম্বির থেকে বানানো পিঠা, লাকড়ির আগুন, মাটির চুলা ও তাওয়ায় ছেঁকার পর যে ঘ্রাণ বের হয় সে ঘ্রাণ বের হয় না আধুনিক পাঁচতারকা হোটেলের ব্যুফে খাবারেও।
শাবান মাসের আরেক নাম তাওয়াপিঠার মাস। মা-বোনেরা ধান কাটার মৌসুমেই তাওয়াপিঠার জন্য আলাদা করে ধান রাখতেন। বিলের চূড়ায় আমাদের যে দুইটা জমি সে দুইটা জমিতে বাবারা বুনতেন লেঞ্জা আমন। বীজ বাছাই করে লেঞ্জা আমন সবটাই রেখে দিতেন তাওয়াপিঠা, চিড়া-মুড়ি ও জ্বালার জাউয়ের জন্য। আমাদের পরিবারে ১২ মাস মুড়ি-চিড়াসহ পিঠা খাওয়ার প্রচলন ছিল। বাঙালি সনাতন সম্প্রদায়ের ছিল ১২ মাসে ১৩ পার্বণ আর বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের ছিল ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, ঈদে মিলাদুন্নবী, শবেকদর ও শবেবরাত। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও উৎসবমুখর পরিবেশে একসময় দিনগুলো পালিত হয়ে আসছিল।
ধর্মীয় সংস্কৃতি আলোচনার আগে ‘সংস্কৃতি’ বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক। সংস্কৃতি বা ঈঁষঃঁৎব শব্দের আভিধানিক অর্থ, কৃষ্টি বা চিৎপ্রকর্ষ। আর লোকসংস্কৃতি হলো, লোকসম্প্রদায় বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে চলতে থাকা ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবন ধারণ প্রণালী এবং চিত্তের উন্নতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি। দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা কোনো বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবনধারণ প্রণালী যখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিজস্ব হিসেবে গ্রহণ ও মূল্যায়নসহ আবশ্যক মনে করতে শুরু করে তখনই হয়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি।
পাশাপাশি অবস্থানহেতু বেশ কিছু লোকসংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাতে শুরু করে। শতবর্ষ থেকে চলে আসা আমন ধান ঘরে ওঠার পর পৌষপার্বণ, শীতকালে জ্বালাপিঠার জাউ, আরবি শাবান মাসে তাওয়াপিঠা, জমিতে প্রথম বীজ ফেলতে ‘বিচুত’, প্রথম হাল শুরুর আগে লাঙলে সোনারুপার পানি ছিটানো ও বাংলা পয়লা বৈশাখে নববর্ষ সবই লোকসংস্কৃতি। চিত্তবিনোদনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে লোকসংস্কৃতি যেমন- নববর্ষ বা ‘পয়লা বৈশাখ’। এই একটি মাত্র দিনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকতাম সারা বছর। নববর্ষকে আমরা বলতাম ‘গাছতলা’। গাছতলা বলার কারণ, কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে আমাদের এলাকা- যা দেশের মূল ভূখ- থেকে মেঘনা ও কাঁঠালিয়া নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যভাগে বৈদ্যনাথপুর। বৈদ্যনাথপুর এলাকায় বিশালাকারের বটগাছের তলায় নববর্ষের মেলা জমত। তাই নামকরণ হয়েছে ‘বৈদ্যনাথপুরের গাছতলা’। কাঠের নড়বড়ে-ভাঙা সাঁকোর ওপর দিয়ে বৈদ্যনাথপুরের গাছতলা যাওয়ার জন্য ১২ মাস পয়সা জমাতাম। নানা রকমের খেলাসহ বাঁশি, বেলুন, বরইর ভর্তা, জিলাপি, খই-মুড়ি এবং মেয়েদের জন্য আলতা, আতর, স্নো-পাউডার, মাথার সিঁথিপাটি ছিল মেলার প্রধান আকর্ষণ। বাঁশির শব্দে এলাকা মাতিয়ে নতুন পাতিলে করে কিংবা মোর্তার রশিতে ঝুলিয়ে জিলাপি নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। কখনো কখনো বৈশাখি ঝড়ের কবলে পড়ে অর্ধেক খই-জিলাপি পথেই ফেলে আসতে হয়েছে। ফসলের সাথে জড়িত কোনো কোনো লোকজসংস্কৃতির সাথে যোগ হয়েছে মিলাদ-মাহফিল, দোয়া-দরূদ ও দান-খয়রাত; যেমন, বিচুতের সময় বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাসহ মসজিদ থেকে ইমাম সাহেবকে ডেকে দোয়া করা হয়। শাবান মাসে দান-খয়রাত অধিক পুণ্য। তাই, তাওয়াপিঠা প্রস্তুতের সাথে কোনো একসময় যুক্ত হয়ে পড়েছে জোড়াপিঠা দান-খয়রাতের বিষয়টি। এভাবেই হাজার বছর থেকে চলে আসা বাঙালির চিরায়ত লোকসংস্কৃতিরই কিছু অংশ এক দিন মুসলিম বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ে। যেহেতু আমাদের এক পরিচয় মুসলমান আরেক পরিচয় বাঙালি, সেহেতু চিরায়ত লোকসংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালিসংস্কৃতির মন, মানস ও অস্তিত্ব। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় গৃহপালিত হাঁস-মুরগি ছাড়া পোলাও-গোশতের প্রচলন তেমন শুরু হয়নি। গ্রাম এলাকায় ঈদুল আজহা ও বড় মেহমানি ছাড়া গরু জবাই খুব একটা চোখে পড়ত না। বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের এসব পার্বণ উপলক্ষে মেয়েরা জামাই নিয়ে বেড়াতে আসে বাপের বাড়ি। মহাধুমধাম করে নারকেল-গুড়ের মিষ্টান্ন কিংবা হাঁস-মুরগির ঝোল মিলিয়ে চলতো তাওয়াপার্বণ। তাওয়াপার্বণে নতুন জামাইকে লুঙ্গি ও মেয়েকে কাপড় দেয়ার রেওয়াজ ছিল। শাবান মাসে প্রচুর তাওয়াপিঠার আশায় বেড়ে যায় মৌসুমি ভিখারির সংখ্যা। এ সময় ভিখারিরা এত বেশি পরিমাণ পিঠা পায় যে, কিছু পিঠা শুকিয়ে সংরক্ষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমরাও দান-দক্ষিণার পর অবশিষ্ট পিঠা শুকিয়ে রাখতাম। শুকিয়ে রাখা পিঠা দিয়ে প্রথম রোজায় ইফতার করা হয়। শুষ্ক তাওয়াপিঠা আবার তাওয়ায় সেঁকলেই হয়ে ওঠে মচমচে। মচমচে পিঠা কিংবা গুড় নারিকেলের মিষ্টান্নে ডুবিয়ে ইফতার করার স্বাদ আধুনিক হালিমে পাওয়া যায় না।
শাবানের চাঁদ উঠলেই মনে পড়ে তাওয়াপিঠার কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফেলে আসা স্মৃতি। প্রথাগত নিয়ম ঠিক রাখতে গিয়ে বাজার থেকে আতপ চাল কিনে মেশিনে আটা বানিয়ে কিংবা দু-চার কেজি ময়দা দোকান থেকে নিয়ে রুটি বানানো হয়। এতে জিহবার তৃপ্তি ও মনের আকাক্সক্ষা কোনোটাই নিবৃত্ত হয় না। আকাক্সক্ষা নিবৃত্তির জন্য বছর দশেক আগে গ্রামে গিয়েছিলাম। শবেবরাতের দিন গ্রামে গিয়ে হাঁটলাম সারা গাঁ। কারো বাড়িতে চালের গুঁড়ি দেখলাম না। শহরের মতোই মেশিনে পেষা আটার রুটি ও নানা প্রকার হালুয়া। কেউ কেউ বাজার থেকে কিনে নিয়েছে তৈরি রুটি। হাতি-ঘোড়াসহ কুমিরাকৃতির মতো রুটি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, এই জীব-জানোয়ারের আকৃতির রুটি দিয়েই শেষ করে তাওয়ার কাজ। মধ্য শাবান অর্থাৎ পূর্ণিমা রাতে শবেবরাত। এই রাতকে আরবিতে ‘লাইলাতুল বারাআত’ বলা হয়। বারাআত অর্থ নিষ্কৃতি। মুসলমানদের বিশ্বাস, এই রাতে বহুসংখ্যক বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও আশীর্বাদ লাভ করে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। গাঁও-গেরামে পূর্ণিমা রজনী এমনিতেই উৎসবমুখর, এর উপর দিনের বেলায় তাওয়াপিঠা, রাতের বেলা নিষ্কৃতি- একেবারে সোনায় সোহাগা। তাই শৈশব থেকে এই রাত স্মরণীয় ও বরণীয়।
শৈশবে দেখতাম, শবেবরাতের দিন সন্ধ্যায় কাকা মোহাম্মদ আলী ও ফুফা হাজী আসমত আলী সাহেব আমাদের বাড়ি আসতেন। বাড়ির মহিলারা একত্র হয়ে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে তাঁদের কাছে শবেবরাত নামাজের নিয়মকানুন শিখতেন। তাদের বিশ্বাস, সারা বছর সাংসারিক টানাপড়েনসহ কাজের চাপে আল্লাহ-রাসূল সা: এর আদেশ-নির্দেশ ঠিকমতো পালন করতে পারছেন না। আদেশ-নির্দেশ অমান্য করার কারণে কত পাপ জমা হয়েছে, লেখা-জোখা নেই। পরম দয়ালু করুণাময় স্রষ্টার অশেষ দয়া এই রজনী। এই রজনীতে স্রষ্টার অশেষ দয়া ও মেহেরবানিতে নিজেদের অক্ষমতার কথা মনে করে রোনাজারির ফলে চোখে জল নামলে সব পাপ-গ্লানি ধুয়ে-মুছে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাই বাড়ির সব মহিলা একত্র হয়ে ফুফা ও কাকার কথা শুনতেন। পাশে দাঁড়িয়ে আমরাও শুনতাম মনোযোগ দিয়ে। তাদের মুখে শুনতাম, শাবান মাসের ১৪ দিবাগত রাতে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর খুব কাছাকাছি নেমে আসেন এবং অসংখ্য গুনাহগারের গুনাহখাতা মাফ করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব কিতাব খুলে পাঠ করে শোনাতেন, শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে ফার্সি ভাষায় শবেবরাত বলে। শব অর্থ রাত আর বরাত অর্থ মুক্তি। অর্থাৎ মুক্তির রাত। এ রাতে আল্লাহ মুক্তি ও মাগফিরাতের দরজা খুলে দেন। সূরা দুখানের ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে “নিশ্চয়ই আমি উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে। … সেই বরকতময় রাতে প্রজ্ঞাময়তা দ্বারা (সত্য ও মিথ্যার) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালা করা হয়।” অধিকাংশ তাফসিরে এই রাত্রকে ‘শবে কদর’ হিসেবে চিহ্নিত করলেও কোনো কোনো তাফসির যেমন- আল-জালালাইন শরিফে বিখ্যাত সাহাবি হজরত ইকরামা (রা:) বলেন, ‘ফয়সালার রাতই হয়েছে, অর্ধ শাবানের তথা ১৫ শাবানের রাত। এই শবেবরাতে সামনের এক বছরের যাবতীয় কিছুর ফয়সালা করা হয় এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয় মৃত ও জীবিতদের। এই রাতে যার যার ভাগ্যে যা কিছু লেখা হয় তা থেকে কোনো কমতিও করা হয় না এবং কোনো কিছু বেশিও করা হয় না (তফসিরে কুরতুবির ১৬তম খ-ের ১২৬/১২৭ পৃষ্ঠা)’ “অথবা লাইলাতুম মুবারাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ শাবানের রাত (তফসিরে জালালাইন শরিফ ৪১০ পৃষ্ঠা)।’ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজ থেকে পূর্ণ কুরআন একত্রে অবতরণ করেন শবেবরাতে। আর অবতরণের ধারা সমাপ্ত করেন শবেকদরে।’ শবেবরাতের নানা রকম ফজিলতের বিষয় শুনতে শুনতে এমনই মুগ্ধ হয়ে যেতাম যে, অধিক পুণ্যের আশায়, নামাজ শুরু করার আগে ঠা-া পানিতে গোসল করতাম। তখন সারা গাঁয়ে একটিমাত্র মসজিদ। মসজিদের ভেতরে মানুষের ঠাঁই হতো না, চট বিছিয়ে বাদাম (পাল) টাঙিয়ে উঠান আঙ্গিনাও ভরে উঠত মানুষে মানুষে। ঘুম ঘুম ভাব কাটানোর জন্য কিছুক্ষণ পর পর উচ্চকণ্ঠে দরূদ, “ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা…” বলে দাঁড়ালে ঘুম ছুটে পালাত। তারপর চা-বিস্কুটসহ আমৃত্তি জিলাপিতো আছেই। এ রকম উৎসবমুখর পবিবেশে কাটত শৈশবের শবেবরাতের রাতটা। ১৯৮৫ সালের দিকে ঢাকা কোর্টে আগমন। চাকরি ছেড়ে আইন পেশায়। মহাদুঃসময়। মহাদুঃসময়ে ভাগ্যবদলের রজনী শবেবরাতের সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না কিছুতেই।। তখন আমি দয়াগঞ্জ এক বন্ধুর বাসায়। বাড়ি থেকে আমার এক কাজিন আসেন। তাকেও রেখে দিই শবেবরাত রজনীটি আমাদের সাথে শেয়ার হওয়ার জন্য। দিনে করা ছক অনুসারে রাত ১০টার দিকে যাই বায়তুল মোকাররম মসজিদে। দূর থেকেই বুঝতে পারি, মসজিদ লোকে লোকে লোকারণ্য। ভেতরে প্রবেশ করে সাধ্য কার! মানুষের ভিড় দেখে মনে সন্দেহ জাগে যে, আমাদের কেউ হারিয়ে যেতে পারি। হারিয়ে গেলে সীমাহীন দুর্ভোগসহ আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। তাই আমার প্রস্তাব ছিল, কেউ হারিয়ে গেলে কোনো এক নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করতে হবে। নির্ধারিত স্থান থেকে সংগ্রহ করে আবার এক হয়ে যাবো। স্থান চিহ্নিত করার আগেই আমার প্রস্তাব সহাস্যে উড়িয়ে দিলেন কাজিন। উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘আমরা কি নাবালক যে হারিয়ে যাবো!’ এ কথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে যায় কাজিন। ঘণ্টা দেড়েক পঁইপঁই করে খুঁজেও কাজিনের শুলুক-সন্ধান পেলাম না। মন খারাপ করে রাত ১২টার দিকে রওনা হই হাইকোর্ট মাজার মসজিদে। আমার ঢাকাইয়া বন্ধু মাজারভক্ত। হাইকোর্ট এলাকায় মাজারও দেখা হবে, নামাজও আদায় করা হবে। যাওয়ার পথে রিকশা, ভ্যান এমন কি ঠেলাগাড়ি ভর্তি উঠতি বয়সী যুবক। সবাই উচ্চস্বরে দোয়া-দরূদ পাঠ করতে করতে এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে যাতায়াত করছে। রাত দেড়টার দিকে যাই আজিমপুর গোরস্তান। হাজার হাজার মানুষ গোরস্তানে। কেউ দোয়া করছে, কেউ জোরে জোরে পাঠ করছে দরূদ। দোয়া-দরূদের মধ্যেই কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রোদন করছে। আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে টুপি মাথায় সফেদ-শুভ্র সাজে এই অভাবনীয় দৃশ্য বর্ণনার ভাষা নেই। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ভেসে যাচ্ছে শহর। এই অভাবিত দৃশ্য কেবল শবেবরাতের রাতেই দেখা যেত। (অসমাপ্ত) লেখক : আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক।